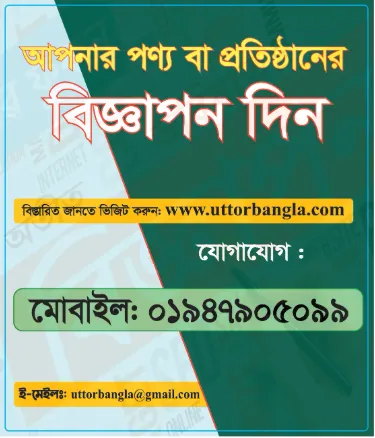
ফারহানা ইয়াসমিন
উত্তরাঞ্চলের মানুষের জীবনে তিস্তা নদী এক বিশাল আবেগের নাম। বর্ষার বন্যায় সব কিছু ভাসিয়ে নেওয়া আর শুষ্ক মৌসুমে পানিশূন্যতার অতল ফাঁদ—এই দুই চরম অবস্থার মাঝেই তিস্তার তীরের মানুষের জীবন চলে দীর্ঘদিন ধরে। নদীর বুক শুকিয়ে যাওয়া, নাব্যতা হারানো, চর জেগে ওঠা, আর ফসলহানির দুঃসহ অভিজ্ঞতা যেন তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই বাস্তবতায় বহু দিনের স্বপ্ন “তিস্তা মহাপরিকল্পনা” আবারও আলোচনায় ফিরে এসেছে। নদী, মানুষ, রাজনীতি ও কূটনীতির জটিল সমন্বয়ে এই পরিকল্পনা এখন শুধু একটি প্রকল্প নয়—এটি হয়ে উঠেছে উত্তরাঞ্চলের আশা ও রাষ্ট্রীয় কৌশলের প্রতীক।
তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৮৩ সালে দুই দেশ একটি অন্তর্বর্তী চুক্তিতে পৌঁছেছিল, যেখানে শুষ্ক মৌসুমে ৩৬ শতাংশ পানি পাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের। পরে ২০১১ সালে আরও শক্তিশালী একটি স্থায়ী চুক্তির খসড়া তৈরি হয়, তাতে বাংলাদেশের বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৩৭.৫ শতাংশ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপত্তি জানানোয় সেই চুক্তি থেমে যায়। তারপর থেকে তিস্তা ক্রমে হয়ে ওঠে দুই প্রতিবেশী দেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েনের একটি প্রধান উপাদান।
এমন অবস্থায় বাংলাদেশ অপেক্ষায় না থেকে তিস্তার নদী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে নতুন পথ খোঁজে। ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান POWERCHINA-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে নদী খনন, নাব্যতা বৃদ্ধি, তীর সংরক্ষণ, জমি পুনরুদ্ধার, নৌপথ উন্নয়নসহ বড় পরিসরের পুনর্বাসন পরিকল্পনার কথা বলা হয়। ধারণা করা হয়, প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াতে পারে প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চীনের অংশগ্রহণে ভারতের কৌশলগত উদ্বেগ দেখা দিলেও বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বিকল্প দরজা খুলে দেয়—যা দীর্ঘ জলবণ্টন জটিলতার মাঝে নতুন বাস্তবতায় পরিণত হয়।
তবে এই পরিকল্পনা শুধুই আন্তর্জাতিক রাজনীতির গল্প নয়। তিস্তা তীরের মানুষের জীবনে এটি পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি বহন করে। প্রতি শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানি কমে যাওয়ায় রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও নীলফামারীর হাজারো কৃষক জমি চাষ করতে পারেন না। নাব্যতা হারানোয় নৌচলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। নদীভাঙনে বছরের পর বছর মানুষ গৃহহারা হয়; চর জেগে ওঠে আবার হারিয়েও যায়। অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ—সব দিক থেকেই তারা একটি স্থায়ী সমাধানের অপেক্ষায়।
কিন্তু প্রকল্পকে ঘিরে রয়েছে পরিবেশগত আশঙ্কাও। বিশাল আকারের খনন, বাঁধ নির্মাণ এবং জমি পুনরুদ্ধার নদীর প্রাকৃতিক গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে—এমন সতর্কবার্তা দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা। নদীর তলদেশ থেকে অতিরিক্ত স্লিট সরানো কিংবা কংক্রিট কাঠামো নির্মাণ হলে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। ভূগর্ভস্থ পানিস্তরেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের কারণে রাজনৈতিক বিতর্কও প্রকল্পটিকে ঘিরে বেড়ে উঠছে।
এর মাঝেই নতুন অগ্রগতি এসেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তিস্তা মহাপরিকল্পনার প্রথম আনুষ্ঠানিক যৌথ সমীক্ষা শুরুর কথা জানিয়েছে সরকারি দপ্তর, যা চলবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। সমীক্ষা শেষ হলে নকশা, অর্থায়ন, পরিবেশগত মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ধাপে ধাপে এগোবে। তবে অর্থায়ন, কূটনৈতিক ভারসাম্য, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং পরিবেশগত অনুমোদন—চারটি প্রধান চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম না করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন দেরি হতে পারে বলে মনে করছেন নীতি–বিশ্লেষকরা।
তবুও নদীর ধারেকাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের স্বপ্ন থেমে নেই। তাদের বিশ্বাস—তিস্তা একদিন আবার ভরপুর হবে, নদীর বুক দিয়ে নৌকা চলবে, ফসল ভরবে মাঠে, আর নদীভাঙনে হারানো ঘরবাড়ি আবার ফিরে পাবে স্থিতি। তাদের জন্য তিস্তা মহাপরিকল্পনা শুধু একটি উন্নয়ন প্রকল্প নয়—এটি বাঁচার গল্প, টিকে থাকার লড়াই, এবং ভবিষ্যতের প্রতি গভীর এক আকুতি।
লেখক: শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ,বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।