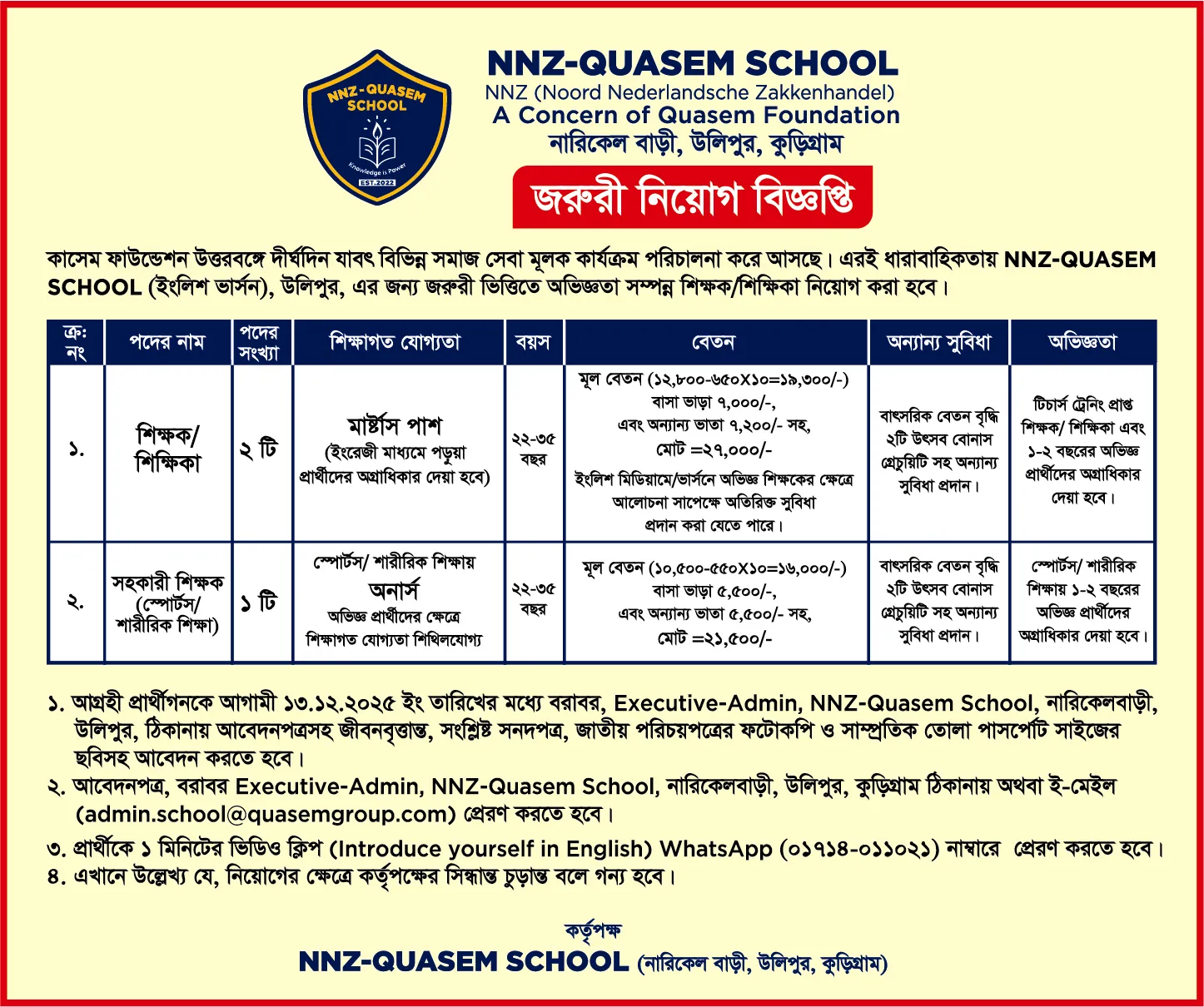
অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ || একটা সময় ছিল চিকিৎসক মানেই ত্রাণকর্তার মতো কেউ, যাঁর কাছে মানুষ আশ্রয় খুঁজত, ভরসা রাখত, প্রাণ বাঁচানোর আকুতি জানাত। সেই পেশাটা আজ এমন এক দিকচিহ্নহীন পথে হাঁটছে, যেখানে রোগীর আরোগ্য নয়, বরং মুনাফাই হয়ে উঠেছে চূড়ান্ত গন্তব্য।
যে সমাজে জীবন বাঁচানো পেশা হয়ে ওঠে মুনাফার কারখানা, সে সমাজের রোগ কেবল শরীরের নয়, অন্তরেরও। এই বাক্যটি এখন নিছক কবিতার পঙ্ক্তি নয়, সময়ের এক নির্মম বাস্তব প্রতিচ্ছবি।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বর্তমানে যে ‘ত্রিশূলের ত্রাস’ কাজ করছে চিকিৎসক, টেস্ট ও ওষুধ- তা শুধু রোগীদের পকেট নয়, বিশ্বাসও নিঃশেষ করে দিচ্ছে। একজন সাধারণ নাগরিক যখন অসুস্থ হন, তখন তার প্রথম প্রত্যাশা হয় সাশ্রয়ী ও সৎ চিকিৎসা। কিন্তু আজ সেই প্রাথমিক মানবিক চাহিদাটিই একশ্রেণির পেশাজীবীর কাছে হয়ে উঠেছে অমানবিক বাণিজ্য।
রোগ নয়, টেস্টের ফাঁদ : চিকিৎসকের চেম্বারে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় এক অদৃশ্য কিন্তু বহুল চর্চিত খেলা। রোগীকে দেওয়া হয় দীর্ঘ টেস্টের তালিকা, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। এসব টেস্ট রোগী যেখানেই করান না কেন, নির্দিষ্ট কমিশনের একটা অংশ পৌঁছে যায় চিকিৎসকের হাতে। এ যেন এক ‘খোলা গোপনীয়তা’, যা সবাই জানে, কিন্তু কেউ উচ্চারণ করতে চায় না।
টেস্টের পর আসে প্রেসক্রিপশন। অথচ এটিও এখন পরিণত হয়েছে কমিশন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে। অধিকাংশ চিকিৎসক রোগীকে নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ লিখে দেন। ওষুধ কোম্পানিগুলো সেই চিকিৎসকদের জন্য সাজিয়ে রাখে নানান সুবিধা ঘরবাড়ি, গাড়ি, বিদেশভ্রমণ, অনৈতিক আরো কিছু। কিছু কোম্পানির প্রতিনিধিরা তো আবার হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং চিকিৎসকের চেম্বারের সামনেই বসে প্রতিটি প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলে পাঠান হেড অফিসে, এই ‘টার্গেট পূরণ’ নিশ্চিত করতে! এটা কেবল একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতা নয়, নীতিহীনতার সাংগঠনিক রূপ- যেখানে চিকিৎসা আর মানবতা নয়, লভ্যাংশ আর পারফরম্যান্স গ্রাফই মুখ্য।
ব্যতিক্রম কি একেবারেই নেই? আছে। অনেক চিকিৎসক আছেন, যাঁরা এখনো নিষ্ঠার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। রোগীর প্রতি মানবিক থাকেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় ক’জন? এই ব্যতিক্রমী মানুষদের অস্তিত্ব যেন এখন কেবল ‘উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম’ হয়েই থেকে যাচ্ছে।
সমাধান একটিই জেনেরিক নামের বাধ্যবাধকতা : এই ভয়াবহ কমিশন-সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কঠিন কোনো প্রক্রিয়া প্রয়োজন নেই। সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। একটি সরকারি সার্কুলার দিয়ে নির্ধারণ করে দিতে পারে চিকিৎসকেরা প্রেসক্রিপশনে কেবল ‘জেনেরিক’ নাম ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো ব্র্যান্ডেড নাম নয়।
‘জেনেরিক’ নাম মানে হলো ওষুধের মূল রাসায়নিক উপাদানের নাম, যেমন Paracetamol। অন্যদিকে Napa, Ace, Tylenol এগুলো সব ব্র্যান্ডেড নাম। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশেই এ নিয়ম বহুদিন ধরেই চালু রয়েছে। রোগী তার সাধ্যের মধ্যে আস্থার কোম্পানির তৈরি ওই ওষুধ কিনবেন। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী জেনেরিক নামে ওষুধ কোম্পানিগুলো যাতে ওষুধ তৈরি করে এবং চিকিৎসকরা যাতে কোনো কোম্পানির বদলে প্রেসক্রিপশনে শুধু ওষুধের জেনেরিক নাম লেখেন সে প্রস্তাব করেছিলেন। আঁতে ঘা লাগায় দেশিবিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলো তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল। তবে তদন্তে প্রমাণিত হয় কোনো দুর্নীতিতে তিনি জড়িত ছিলেন না। সবটাই ছিল ওষুধ কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র। কোম্পানিগুলোর মধ্যে গুণগত মানের প্রতিযোগিতা বাড়বে, কমিশনের নয়। প্রেসক্রিপশন হবে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও মানবিক।
নীতি নয়, নৈতিকতার প্রশ্ন : এই সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য নতুন টিম, অর্থ বা প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের প্রয়োজন নেই। কেবল একটি সুস্পষ্ট ঘোষণাই যথেষ্ট : ছয় মাস পর থেকে সব প্রেসক্রিপশনে কেবল ওষুধের ‘জেনেরিক’ নাম লেখা বাধ্যতামূলক। একটি ঘোষণাই পারে হাজারো টেস্ট ল্যাব আর ফার্মাসিউটিক্যাল কমিশনের বিষাক্ত বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে রোগীকে, ফিরিয়ে দিতে চিকিৎসক-পেশার মর্যাদা। চিকিৎসা কখনোই শুধুই একটি পেশা ছিল না; এটি মহান দায়িত্ব, নৈতিক শপথ। রোগীর আরোগ্য হওয়া উচিত একজন চিকিৎসকের কাছে সবচেয়ে বড় ‘পুরস্কার’, কমিশন নয়। চিকিৎসা যদি অর্থের বিনিময়ে বিশ্বাস হরণে পরিণত হয়, তাহলে সেই সমাজ বিবেক হারায়, ভবিষ্যৎও। চিকিৎসক ও রাষ্ট্রের কাছে আমাদের একটাই আকুতি চিকিৎসা যেন মানুষের কাছে ভয় নয়, ভরসার নাম হয়।
লেখক : ওয়ার্ল্ড পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস সোসাইটির চেয়ারম্যান